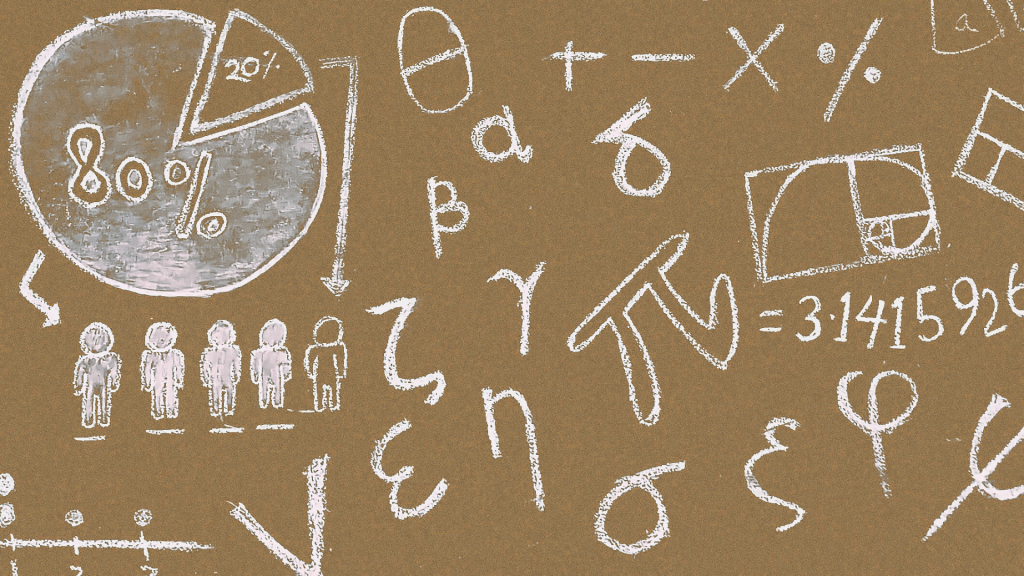২০২০ সালে কোভিড-১৯ এর আগমনের পর বাংলাদেশে একটি নীরব অথচ গভীর পরিবর্তন শুরু হয়। প্রথমবারের মতো দেশের তথাকথিত অনেক ‘জ্ঞানী’—যারা নিজেদের জ্ঞানের ধারক ও বাহক বলে দাবি করতেন—তাদের প্রকাশ্যে প্রশ্ন করতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা। কীভাবে ঘটল এই পরিবর্তন?
কোভিডের আগে অধিকাংশ মানুষের ইন্টারনেট ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল ফেসবুক, ইউটিউব, ভাইবার, ইমো কিংবা মাঝেমধ্যে গুগল সার্চে। অনলাইনকে খুব কম মানুষই গঠনমূলক জ্ঞানের উৎস হিসেবে দেখত। কিন্তু মহামারি যখন পুরো পৃথিবীকে স্তব্ধ করে দেয়, তখন হঠাৎ করেই এক নতুন জিনিস চালু হয়—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে অনলাইন ওয়েবিনার।
যদিও সেমিনার বা আলোচনা সভা আগে থেকেই ছিল, কিন্তু সেগুলো সবই হতো অফলাইনে, সীমিত পরিসরে। বাংলাদেশের খুব কম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই সাহস করত বিদেশি স্কলারদের আনতে, খরচের ভয়ে। কিন্তু কোভিড এই হিসাব বদলে দেয়। বিদেশি শিক্ষাবিদেরা অনলাইনে বিভিন্ন ওয়েবিনারে অংশ নিতে থাকেন, গবেষণা, জার্নাল, রিভিউসহ নানা বিষয়ের গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরেন।
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সামনে হঠাৎ খুলে যায় এক নতুন জগত—গবেষণাধর্মী কঠিন বিষয়গুলো এত সহজ ও স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হচ্ছিল যে তারা ভাবতে শুরু করে, “আসলে এতটা কঠিন তো নয়!”
তারা স্কলারলি আর্টিকেল পড়া শুরু করে, অনলাইন ক্লাস দেখে এবং—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—‘International Standard’ বা আন্তর্জাতিকমানের ধারণা সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে।
এই সচেতনতা তাদের এক প্রশ্নে নিয়ে আসে—আমাদের শেখানো জ্ঞান আসলে আন্তর্জাতিক মানে কোথায় দাঁড়ায়?
তারা খেয়াল করে, বাংলাদেশের একাডেমিক গোষ্ঠীগুলো—যারা যেইপক্ষেই থাকুক না কেন বা যেই পন্থী হোন না কেন—অনেক আগে থেকেই জ্ঞানকে একটি স্থানীয় বা স্বঘোষিত মানদণ্ডের মধ্যে আটকে রাখারচেষ্টা করছিল। প্রাতিষ্ঠানিক অহংকার, পাবলিক বনাম প্রাইভেট বিভাজন, তথাকথিত “পাবলিক জার্নাল”-এ প্রকাশের গর্ব, প্রিন্ট বনাম অনলাইন জার্নালের পক্ষপাত—এসবই মিলে এমন এক কাঠামো তৈরিকরে যার মাধ্যমে তারা নিজেদের মানকে শীর্ষে রেখে দেয়।
কিন্তু এখন শিক্ষার্থীরা অনলাইনে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মানের জ্ঞানের উৎসে প্রবেশ করতে পারছে—তারা আর ওই বদ্ধ মানদণ্ড মানতে চায় না। তারা আন্তর্জাতিক মান খোঁজে—যেখানে কাজের গুণমান ও প্রাসঙ্গিকতাই মুখ্য, প্রতিষ্ঠানের নাম নয়। ফলে তারা দেখতে পায়, আমাদের দেশের অনেক একাডেমিক কাজই আন্তর্জাতিক মান থেকে বহু দূরে।
এরপর আসে আরেকটি বাস্তবতা: কোভিডের পর অনেক শিক্ষার্থী ক্লাসরুমে ফিরে যেতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। কেন? কারণ কোভিড কালে তারা হার্ভার্ড, এমআইটি’র মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের ক্লাস দেখে ফেলেছে—যেখানে ক্লাস মানেই শুধু লেকচার নয়, বরং ওপেন ডিসকাশন, প্রশ্নোত্তর, সমান অংশগ্রহণ, দ্বিধার জন্ম দিয়ে উত্তর খোঁজার চর্চা এবং হাতে-কলমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান যাচাই করার পদ্ধতি।
কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ ক্লাসে এখনো পুরোনো একমুখী লেকচারই “স্বাভাবিক” এবং “গ্রহণযোগ্য” হিসেবে বিবেচিত হয়।
এখন ভাবুন, এক শিক্ষার্থী যদি ২৯৯ টাকা এমবি দিয়ে বা মাসে ৫০০ টাকায় ওয়াই-ফাই কিনে বাসায় বসে ১০–১৫ মিনিটে জটিল বিষয় পরিষ্কার করতে পারে, তাহলে কেন সে ২ ঘণ্টা জ্যাম পেরিয়ে, নিয়মের জঞ্জালে ভর্তি ও বিষাক্ত পরিবেশে গিয়ে ক্লাস করবে? উত্তর সে পায় না। কিন্তু সবসময় সে প্রতিষ্ঠানকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জও করতে পারে না। ফলেহয় সে নিরাসক্ত হয়ে পড়ে, না হয় বিদ্রোহ করে।
এই বিচ্ছিন্নতার জন্য দায়ী কে? দায় তাদেরই—যারা জ্ঞানকে কুক্ষিগত রাখতে চায়।
আজ আমরা আরেকটি নতুন বাস্তবতার মুখে দাঁড়িয়ে। বিশ্বজুড়ে শিক্ষাও গবেষণায় AI বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে দ্রুত জ্ঞান সৃষ্টি এবংসমস্যা সমাধান করা হচ্ছে। অথচ আমাদের অনেকেই এখনো AI এর বিষয়ে অবজ্ঞাসূচক মনোভাব পোষণ করে। আগে একজন শিক্ষার্থীকে ২০টি গবেষণা প্রবন্ধ খুঁজে, ২০টি তত্ত্ব ঘেঁটে, একটি প্রাসঙ্গিক তত্ত্ব বের করতে হতো। এখন AI সহজেই বলে দিতে পারে—কোন তত্ত্ব ব্যবহার করা যায়, তার সীমাবদ্ধতা কী, কোন দিক নিয়ে কাজ করা যেতে পারে।
আগে এই কাজ করতে মাসের পর মাস সময় লাগত, উপরন্তু পরিচিত কোনো ‘বড় স্কলার’ সাহায্য করবে কিনা তা নিয়েও ছিল অনিশ্চয়তা। এখন এই সমস্যাগুলো অনেকটাই নেই। গবেষকরা নির্দিষ্ট সমস্যার ওপর মনোযোগ দিতে পারছেন এবং কার্যকর সমাধান দিচ্ছেন।
কিন্তু একেই ঘিরে তৈরি হয়েছে আরেক ভয়—যেহেতু জ্ঞান এখন খুব দ্রুত তৈরি হচ্ছে, আগের অনেক তত্ত্ব বা মতবাদই হুট করে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। ফলে যাঁরা আগে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা অস্বস্তিতে পড়ছেন। তাই তারা নতুন নতুন বাধা তৈরি করছেন, যেন পরিবর্তনের গতি ধীর হয়। কিন্তু এমন প্রতিরোধ খুব একটা সফল হচ্ছে না।
পৃথিবী এত দ্রুত বদলাচ্ছে যে আগামী ছয় মাস পর কী হবে, তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না।
বাস্তবতা হলো—এই পরিবর্তিত বিশ্বে আমাদের দ্রুত মানিয়ে নিতেহবে। যত দ্রুত মানিয়ে নিতে পারব, আমাদের অবস্থান ততই শক্তিশালী হবে।
না হলে আমরা ঠাঁই পাব হয়তো জাদুঘরে—অথবা হতাশা, বিষণ্ণতা ও বিলুপ্তির গল্পে।
মুহম্মদ মেহেদী রহমান, শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত এবং আলস্যে লেখালেখির অভ্যাসে দুষ্ট।
একসময় বিতর্ক করতেন।